গ্রাম থেকে শহর : প্রয়োজন গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবর্তন

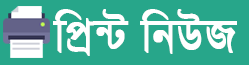
ড. রুশিদান ইসলাম রহমান
গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে উন্নয়ন তত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা বহু বিশ্লেষণ করেছেন এবং এ বৈষম্য হ্রাস করার জন্য সুপারিশ করেছেন। গ্রাম ও শহরের বৈষম্যের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে।
যেটা খুব সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে এ বৈষম্য বাড়লে দেশে সামগ্রিক আয় বৈষম্য বেড়ে যাবে, যেটা বাংলাদেশে অতীতে ঘটেছে। তাতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী নিজেদের অবহেলিত ও বঞ্চিত মনে করবে। গ্রামে বসবাসকারীরা হেয় গণ্য হবে- নিজের শহরবাসীদের বিবেচনায় যা মোটেও কাম্য নয়।
তবে আরও ক্ষতিকর দিক হচ্ছে গ্রামগুলো অনুন্নত হলে দেশের সামগ্রিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার শ্লথ হবে বা যত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, ততটা হবে না। অধ্যাপক মাইকেল লিপটনের বহুল আলোচিত তত্ত্বে তিনি বলেছেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের উন্নয়ন কৌশলে শহরগুলোর প্রতি পক্ষপাত করে, ফলে গ্রামের উন্নয়ন ব্যাহত হয়, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তৈরি হয়, তার তত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু এ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার পর এ বিষয়টি মনোযোগ পেয়েছে।
আমাদের দেশে তো এ বিষয়টির অন্যান্য রূপ দেখা যায়। যেমন ‘গ্রাম্য’ বা ‘গেঁয়ো’ শব্দগুলোতেই একট নিকৃষ্টতার ছাপ রয়েছে। কাজেই এটা আর বিচিত্র কী, যে গ্রামের যারা কিছুটা শিক্ষিত তারা শহরজীবনে আকৃষ্ট হবে এবং সুযোগ পেলে শহরে অভিবাসী হবে ও কালক্রমে স্থায়ীভাবে শহরবাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে সন্তুষ্ট হবে। এছাড়াও শহরমুখী হয়ে গ্রাম ত্যাগ করার অন্য কারণও রয়েছে- যেমন শহরের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি। এটা শিক্ষিত সচ্ছল এবং দরিদ্র বা অশিক্ষিত সবার জন্যই প্রযোজ্য।
অথচ ক্রমাগত গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের কুফল তো এর মধ্যে যথেষ্ট দৃশ্যমান। ঢাকা ও অন্য বড় শহরগুলো অপরিকল্পিতভাবে প্রসারিত হচ্ছে এবং জনজীবন বিপর্যন্ত হচ্ছে। অভিবাসীদের বিশেষত নিু আয়ের যারা, তাদের জীবনযাত্রার মান সামগ্রিক বিবেচনায় খুব যে উন্নত হচ্ছে তা নয়।
কাজেই এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে গ্রামে ও শহরের মতো নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে, গ্রামীণ মানুষ যেন তাদের নিজস্ব জীবনভঙ্গির গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে এটা শুধু গ্রামে সুবিধা বাড়ান হচ্ছে এভাবে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তারা দেশের অর্থনীতির দ্রুততর প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে, গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোতে, পরিবর্তনের মাধ্যমে- সেই কৌশলের অংশ হিসেবে নেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে।
এ প্রক্রিয়ার অর্থ কি গ্রামকে শহর হিসেবে গড়ে তোলা, নাকি গ্রামকে ‘উন্নত গ্রাম’ বা নাগরিক সুবিধা সম্বলিত গ্রাম বলা হবে সেটা নিয়ে বির্তক হচ্ছে। তবে মূল বিষয়টি হচ্ছে গ্রাম উন্নতর হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা বাড়বে, প্রবৃদ্ধি বাড়বে, প্রযুক্তি উন্নতর হবে- যাতে দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়ে উচ্চমধ্যম আয়ের স্তরে নিয়ে যাবে দেশকে। সঙ্গে অধিকতর কর্মসংস্থানও হবে গ্রামীণ এলাকাতে।
এ লক্ষ্য সামনে রেখে গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন সেটা আলোচনা করা যাক। শুরুতেই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গত দুই দশকে বাংলাদেশের উৎপাদন কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, জিডিপিতে কৃষির অংশ কমে এসেছে ১৮.৮, ১৮ ও ১৪.২ শতকরাতে যথাক্রমে ২০০৩, ২০১১ ও ২০১৭-তে। তবে শুধু গ্রামাঞ্চলের জন্য হিসেব করলে গ্রামীণ মোট আয়ের একটি বড় অংশ এখনও কৃষি থেকে আসছে। ২০১০ সালে এ অংশ ছিল ৩৩ শতাংশ (সারনি ১ এর তথ্য)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই তথ্য ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের খানাভিত্তিক তথ্য পুনর্বিশ্লেষণ করে হিসাব করেছিলাম। যদিও তারপরে আরও একটি (২০১৬ সালে) জরিপ হয়েছে, গ্রাম ও নগরের জন্য পৃথকভাবে এ বছরের জন্য খাতভিত্তিক অংশ নিরূপণ করেনি কেউ কোনো গবেষণাতে।
সারনি-১ : গ্রামীণ জনগণের আয়ের খাতভিত্তিক বণ্টন
খাত শতকরা (%)
কৃষি (শষ্য) ২৭.৮
কৃষি (অন্যান) ৫.৬
শিল্প উৎপাদন ৮.৯
নির্মাণ ৩.০
বাণিজ্য ১১.২
যাতায়াত ৫.৫
সেবা ৭.২
রেমিট্যান্স ১৬.৯
অন্যান্য ১৩.৯
মোট ১০০.০
উৎস : খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০-এর তথ্য
গ্রাম ও শহরের জন্য তুলনীয় খাতভিত্তিক আয়ের অংশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থাকা প্রয়োজন, গ্রাম উন্নয়নের সুষ্ঠু পদক্ষেপ নেয়া ও সেগুলোর মূল্যায়নের জন্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অবিলম্বে এ ধরনের তথ্য সরবরাহের জন্য উদ্যোগ নিতে পারে।
মূল প্রসঙ্গে ফিরে এসে যা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কী ধরনের পরিবর্তন কাক্সিক্ষত ও কীভাবে তা সম্ভব, যার ফলে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিবাসনের আকর্ষণ হ্রাস পাবে।
উপরের সারনি থেকে দেখা যাচ্ছে, যে গ্রামীণ পরিবারের আয়ের মাত্র নয় শতাংশের উৎস হচ্ছে শিল্প, এগারো শতাংশের জন্য এটা বাণিজ্য। এখানে আরও একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা জরুরি। গ্রামীণ শ্রমশক্তির শতকরা ৫১.৭ ভাগই কৃষিতে নিয়োজিত (২০১৭ সালে)। এ সঙ্গে আর একটি পরিসংখ্যান সংযোজন করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পরিবারেই শস্য কৃষির থেকে কিছু আয় পাচ্ছে। অর্থাৎ সবদিক মিলিয়ে কৃষির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর বিগত বছরগুলোতে কৃষি খাতে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
কিন্তু তবু এটা অনস্বীকার্য যে শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতি এগিয়ে যেতে পারবে না। এ খাতে জনপ্রতি উৎপাদন বা আয় আধুনিক শিল্প বা সেবাখাতের চেয়ে কম হবে। আর শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে কথোপকথনে তাদের যে মনোভাবটি প্রকাশ পায় তা হচ্ছে গতানুগতিক কৃষি কাজ, তেমন সম্মানজনক পেশা নয় ‘চাষী’ (বা কৃষক) শব্দটিই তো আমাদের কাছে একটু পশ্চাদপদ পেশার ধারণা দেয়। সুতরাং কৃষিকে একটি আধুনিক এবং গতিশীল পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তরুণদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে হলে। আধুনিক কৃষি উদ্যোক্তারা নতুন, উচ্চমূল্যমানের শস্য উৎপাদন করবে, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করবে।
সেসঙ্গে ভাবতে হবে গ্রামীণ শিল্প খাত কী ধরনের হবে এবং কীভাবে সেটার প্রসার ঘটান যায়। এখানে একটু উল্লেখ করা ভালো হবে যে গ্রামীণ শিল্প বলতে আসলে সেটা একেবারে গ্রামের সীমার ভেতরেই স্থাপিত হতে হবে তা নয়।
গ্রামের অধিবাসীরা তাদের গ্রামে বসবাস করেও সেসব শিল্পে কর্মনিয়োজন পায়- হোক সেগুলো আশপাশের ছোট শহরে বা গ্রামে, সেগুলোকে গ্রামীণ শিল্প হিসেব অন্তর্ভুক্ত করা হয় সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে। অতীতে অবশ্য গ্রামীণ শিল্পখাত ছিল খুব ছোট। শুধু গ্রামের মধ্যে, বা নিজ বসতবাড়ির একটি অংশে হস্তচালিত তাঁত বোনা তেলের ঘানি, বাঁশবেতের বা মাটি, পিতলের তৈজস প্রস্তুত- এসব ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখন ভাবতে হবে নতুন প্রযুক্তিনির্ভর, ক্রমবর্ধমান পুঁজি ও শ্রম নিয়োজনকারী শিল্পকে উৎসাহিত করার বিষয়টি। এ শিল্পগুলো হবে গ্রামের কাছাকাছি তবে কোনো পাকা সড়কের সংলগ্ন, তা সেটা কোনো গ্রাম হোক বা নগর হিসেবে চিহ্নিত হোক।
পাকা সড়কের কাছাকাছি হতে হবে, যাতে পণ্য পরিবহন সহজ হয়। আর আজকাল সড়ক জাল তো গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসারিত। সেখানে শ্রমসুলভ হবে- কারণ আশপাশের গ্রাম থেকে তারা আসবে- তেমন যাতায়াত ব্যয় হবে না, নতুনভাবে বসবাসের ব্যয় হবে না।
তাহলে উদ্যোক্তারা এ সুবর্ণ সুযোগটি কেন গ্রহণ করছেন না? প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আমার আলোচনা হয়েছে এ বিষয়ে। তারা মনে করেন ঢাকা-গাজীপুর এসব এলাকাতে গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া সহজ ও সরবরাহে নির্ভরযোগ্য। দূরবর্তী এলাকাতে সেটা নয় তাছাড়া নিরাপত্তা প্রশ্ন, উচ্চতর পরিবহন ব্যয়, এগুলোও আছে। এসব দিকে অগ্রগতি হচ্ছে তবে সেটা দ্রুততর হলে দূরবর্তী এলাকায় শিল্প স্থাপনে আগ্রহ বাড়বে। গত পাঁচ-ছয় বছরে সামগ্রিকভাবে দেশে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান স্তিমিত হয়েছে। আমার কিছু গবেষণাতে দেখিয়েছি যে এ প্রবণতার কারণ হচ্ছে শিল্পখাতে পুঁজিঘনত্ব বৃদ্ধি। শ্রম অসন্তোষ, মজুরি ব্যয় বৃদ্ধি এবং পণ্যের মানোন্নয়নের ফলে কমছে কর্মসংস্থান ও পুঁজির অনুপাত। উদ্ধৃত শ্রমের দেশে এ প্রবণতাটির ফলে বেকারত্ব হার বেড়ে যেতে পারে।
গ্রামাঞ্চলে ও বিভিন্ন এলাকাতে শিল্পোন্নয়ন হলে দ্রুততর হারে কর্মসংস্থান হতে পারে। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন সেবা খাতেরও একটি বিশাল ভূমিকা থাকতে পারে এরকম বিস্তৃতভাবে কর্মসংস্থান তৈরিতে। তবে তরুণদের জন্য উপযুক্ত শিল্প ও সেবাখাতে কর্মসংস্থান বা আধুনিক সেবাখাতে স্বনিয়োজন, এসবের জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা এবং উদ্যোক্তা তৈরির জন্য উপযুক্ত সহায়তা (দক্ষতা ট্রেনিং, উপকরণ, ব্যবসা-নীতিজ্ঞান)। বাংলাদেশে গত দু’তিন দশকে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। কিন্তু সেই শিক্ষার মান যে দুর্বল এবং ক্রমে আরও অবনতি হচ্ছে, তা বহু গবেষণাতেও আলোচনাতে উঠে এসেছে। এ দুর্বলতা গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি প্রকট।
এ প্রসঙ্গে আমার গৃহকর্মে সহায়তাকারী এক নারীর উক্তি উদ্ধৃত করা উপযুক্ত হবে। সে তার রোজগারে দুই ছেলের পড়াশোনার ও বাসাভাড়ার ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে বলে জানাল। আমি পরামর্শ দিলাম, ‘ওদের নিয়ে গ্রামে, যেখানে তোমার বাবা-মা আছেন সেখানে যাও না কেন! তোমার বাসাভাড়া লাগবে না। সরকারি স্কুলে পড়াশোনা হবে বিনা ব্যয়ে’ সে হেসে বলে ‘আপা, বোঝেন তো, শহরের ইস্কুলে বেতন দিয়ে পড়লে যা শিখে, গ্রামের ফ্রি ইস্কুলে তো সেই রকম হয় না। ছেলেদের নিয়ে তো আমার সব আশা।’
কেন গ্রামের সরকারি স্কুলে শহরের মতো মানের শিক্ষা হবে না? পাঠ্যবই পাচ্ছে, স্কুল ঘরও আছে- শুধু দরকার যোগ্য শিক্ষক ও আন্তরিকভাবে শিক্ষাদান। এ বিষয়টি নির্ভর করবে শিক্ষাক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর।
গ্রামে শহরের মতো সেবা প্রাপ্তির অন্যদিকটি হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা বহু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হয়েছে- হিসেব অনুযায়ী শিক্ষিত চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে প্রয়োজনের বেশি। তাহলে কেন গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা উচ্চমানের হবে না? একই বিষয়- সুশাসনের সম্প্রসারণ দরকার।
কাজেই গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোকে গতিশীল করার জন্য, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধির জন্য, ভালো মানের শিক্ষা চাই। ভালো মানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বিকল্প নেই। গ্রাম থেকে শহরের মতো সুবিধা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি উদ্যোগ শুরু হচ্ছে সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ উদ্যোগে অগ্রসর হওয়ার সময়ে কিছু ঝুঁকির বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
এমন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে- এ আলোচনার বিষয়ে সবাই অবগত। কাজেই কিছু তৎপরতা শুরু হবে। যেমন- গ্রামের জমির দাম বাড়বে দ্রুত হারে- গ্রাম যদি শহর হয়ে ওঠে, জমি হবে আরও দুর্লভ। কাজেই গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা, এমনকি শহরের লোকজনও জমি কেনাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। ক্ষুদ্র জমির মালিকরা দূর ভবিষ্যৎ না ভেবে একটু বেশি দাম পেলে জমি বিক্রয় করবেন- এবং পরে হাহুতাশ করবেন। এ প্রক্রিয়াটি কীভাবে ঠেকানো যায় ভাবতে হবে।
অনেকে হয়তো ভাড়া দেয়া যাবে এই আশায় পাকা ইমারত তৈরি করবেন। তাতে পরিবেশবান্ধব নয় এবং অপরিকল্পিত গৃহায়নের কুফল দেখা দেবে। পরিকল্পিত গৃহায়নের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে শুরুতেই। দক্ষ নগর পরিকল্পনাবিদ ও স্থপতিদের পরামর্শ কাজে লাগাতে হবে।
গ্রাম থেকে শহর হওয়ার প্রক্রিয়াতে যেন বৃক্ষনিধন না ঘটে বা বৃক্ষরোপণ নিরুৎসাহিত না হয়- সেদিকে সচেতন দৃষ্টি দিয়ে প্রতি এলাকায় এখন কত বৃক্ষ আছে পাঁচ বছর পরে লক্ষ্য কত, সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে কিনা তার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হবে। সবশেষে উল্লেখ করতে চাই যে, গ্রাম গতিশীল হোক সেটা প্রয়োজন। কিন্তু নগরের যেসব সমস্যা- ধুলাকীর্ণতা, পরিবেশ দূষণ, যানজট এগুলোর অনুপ্রবেশ না ঘটে। যেন ‘ছায়া সুনিবিড়, শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলো’ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করে- সেই প্রত্যাশাই থাকবে।








