মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে বাংলাদেশ মর্মাহত

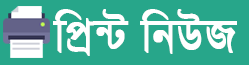
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া : আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে এক ঐতিহাসিক আত্মার সম্পর্ক। ভারতের সঙ্গে রয়েছে আমাদের ইতিহাসের, ভাষার, সংস্কৃতির, মন-মানসিকতার গভীর সমন্বয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৫৪ বছরে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক। বাংলাদেশ-ভারত এর গৌরবময় সম্পর্কের গভীরতা অপরিমেয়। এই দু’দেশের সংস্কৃতি, ধর্ম, প্রথা ও জীবনধারা হাজার বছর ধরে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। দু-দেশের এই সম্পর্কের বীজ বপন হয়েছিল আজ থেকে ৫৪ বছর পূর্বে যখন পূর্ব পাকিস্তান নামক বাংলাদেশের আকাশে কালো মেঘ জমেছিল পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার এবং শোষণের ফলে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতই ছিল বাংলাদেশের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য মিত্রদেশ। সে সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি লোক সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। দেশটি দীর্ঘ ৯ মাস বাংলাদেশের আশ্রয়প্রার্থী ঐ বিপুলসংখ্যক লোকের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া সারা বিশ্বকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের দুরবস্থা এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার কথা জানিয়েছে। এভাবে বাংলাদেশ সৃষ্টির শুরু থেকে ভারত বাংলাদেশের সাথে অকৃত্রিম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। অন্যদিকে বাংলাদেশও তার অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের সাথে সবসময় একটা সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে।
বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের স্বার্থে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশও বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বশেষ ভারতের ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্ব অন্য রাজ্যগুলোর ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহনের জন্য চারটি রুটের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ। এ চার রুট হলো- চট্টগ্রাম বন্দর-আখাউড়া-আগরতলা, মোংলা বন্দর-আখাউড়া-আগরতলা, চট্টগ্রাম-বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর এবং মোংলা বন্দর-বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর। ২০২১-২২ সালে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ভারত এখন এশিয়ায় বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানির বাজার। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক, বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন, বন্দর ব্যবহার, সীমান্ত হাট ইত্যাদির একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরি হয়েছে। এসব খাত ব্যাপক অর্থনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছে। এ ধরনের সহযোগিতা উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি রোল মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে। দুই দেশের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করায় দুই দেশ এখন যে সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে অতীতের তুলনায় তার পরিধি বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত। দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ এবং ইতিমধ্যে ভারত বাংলাদেশে ঘাটতি পূরণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। অপরদিকে বাংলাদেশ ভারতকে ট্রানজিট ও বন্দরে জাহাজ নোঙরের সুবিধা দিচ্ছে। এছাড়া জ্বালানি, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে অনুমান করা যায় যে, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।
কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনাময় এই সম্পর্কের অবমাননা হয়েছে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্যে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের তিস্তা পানিবণ্টন নিয়ে মমতা বানার্জীর উগ্র বক্তব্যে বাংলাদেশ মর্মাহত ও বাকরুদ্ধ। রাজ্য সরকারের অংশগ্রহণ ছাড়া তিস্তা ও গঙ্গার পানিবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আলোচনা করা উচিত হয়নি বলে উগ্র মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরকালে গত শনিবার গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি নবায়ন ও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার বিষয়ে আশ্বাস দেন নরেন্দ্র মোদি। তিস্তা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য কারিগরি দল পাঠানোর কথাও বলা হয়। তবে এ নিয়ে আপত্তি তুলেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশগ্রহণ ছাড়া তিস্তা ও ফারাক্কার পানিবণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনোরকম চুক্তিতে নিজের তীব্র আপত্তি রয়েছে জানিয়ে মমতা বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থ নিয়ে কোনো আপস করব না।’ দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গত ২৪ জুন চিঠি লিখে তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তার পানি ভাগাভাগি করা সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের মানুষের সেচ ও খাওয়ার জন্য এ পানির প্রয়োজন হয়। অথচ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিস্তার পানিবণ্টন নিয়ে ১৯৮৩ সালে একটি অস্থায়ী চুক্তি হয়। আর ২০১১ সালে তিস্তা চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করে দুই দেশ, যেখানে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের ৪২ দশমিক ৫ শতাংশ ও ভারতের ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ পানি পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থহানির যুক্তি দেখিয়ে এ চুক্তির বিরোধিতা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, পানির ওপর রাজ্যের অধিকার যেহেতু স্বীকৃত, তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি উপেক্ষা করে তিস্তা চুক্তি রূপায়ন কার্যত কেন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে তিস্তার পানিবণ্টন নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা যা বাংলাদেশের জন্য কোনোভাবেই সুখকর নয়। মমতা ব্যানার্জীর এই উগ্র বক্তব্যের ফলে তিস্তা পানিবণ্টনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তাতে বাংলাদেশ অপূরণীয় ক্ষতির আরও বেশি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের স্বার্থের বিপরীতে মমতা ব্যানার্জীর এই বক্তব্যে বাংলাদেশ মর্মাহত।
তিস্তা একটি আন্তর্জাতিক নদী, যা বাংলাদেশ এবং ভারত দুটি দেশেরই অংশ। এটি ভারতের সিকিম থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রংপুর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। পরে তা পদ্মা ও মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তিস্তার অববাহিকা আনুমানিক ১২ হাজার ১৫৯ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। এ নদীটি বাংলাদেশ ও ভারতের তিন কোটির বেশি মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এর মধ্যে দুই কোটির বেশি মানুষ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে তিস্তার অববাহিকায় বসবাস করে। ৪০ লাখ মানুষ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রায় ৫০ লাখ মানুষ সিকিমের অববাহিকায় বসবাস করে। অর্থাৎ তিস্তার ওপর নির্ভরশীল ৭০ ভাগ মানুষ বাংলাদেশে তিস্তার অববাহিকায় বসবাস করে।
তিস্তা নদী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফসল বোরো ধান চাষের জন্য পানির প্রাথমিক উৎস এবং মোট ফসলি জমির প্রায় ১৪ শতাংশ সেচ প্রদান করে। তিস্তা ব্যারাজ প্রজেক্ট বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প। এটাও তিস্তার পানির ওপর নির্ভরশীল। এই প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা যথা- নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট এবং এর ‘কমান্ড এরিয়া’ (আওতাভুক্ত এলাকা) ৭ লাখ ৫০ হাজার হেক্টর বিস্তৃত। তিস্তার সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন-জীবিকা ও অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিস্তা নদীতে ভারতের উজানে পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে বাঁধ, ব্যারেজ, জলবিদ্যুৎসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে তিস্তা নদীর পানির প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই অবকাঠামোগুলো তিস্তার উজানে পানির চাহিদা পূরণ করছে। কিন্তু তা ভাটিতে বাংলাদেশ অংশে তিস্তা নদীতে পানির প্রাপ্যতা দারুণভাবে হ্রাস করেছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গজলডোবা ব্যারেজ নির্মাণের আগে বাংলাদেশের ডালিয়া সীমান্তে তিস্তার গড় বার্ষিক পানির প্রবাহ ছিল ৬ হাজার ৭১০ কিউসেক (ঘনফুট প্রতি সেকেন্ড)। ১৯৯৫ সালে গজলডোবা ব্যারেজ চালু হওয়ার পর তা কমে ২ হাজার কিউসেকে দাঁড়ায়। শুষ্ক মৌসুমে সর্বনিম্ন প্রবাহ ১ হাজার ৫০০ কিউসেক থেকে ২০০-৩০০ কিউসেকে নেমে আসে। এটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ভূপৃষ্ঠের পানির প্রবাহ হ্রাস এবং সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে তিস্তা অববাহিকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর গত এক দশকে প্রায় ১০ মিটার নিচে নেমে গেছে। শুষ্ক মৌসুমে তিস্তা নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় তা সেচের ক্ষেত্রে এবং কৃষি ফলনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসলগুলোর একটি বোরো ধান উৎপাদনে এর প্রভাব ব্যাপক। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা যায়, তিস্তার পানির ঘাটতির কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ১৫ লাখ টন বোরো ধান উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে। এটা দেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯ শতাংশের সমান যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয়।
সুতরাং, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী এমন বক্তব্য খুবই দুঃখজনক। আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে তিস্তার পানি ব্যবহার করার অধিকার ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের কোনো অংশে কম নয় বরং বেশি। মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্যে তিস্তা ব্যবহারে বাংলাদেশের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনের বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত ঐতিহাসিক সেই সম্পর্কে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের নিকট বাংলাদেশের আবদারের যে জায়গাটা ছিল সেটা নষ্ট হয়েছে। মমতার বাংলাদেশবিরোধী তথা তিস্তা পানিবণ্টনবিরোধী এমন বক্তব্য কোনোভাবেই উচিত হয়নি। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশ যেমন নিঃস্বার্থভাবে সবসময় এগিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি ভারতকেও বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষিত হবে সবসময় এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে এগিয়ে আসা উচিত।
লেখক : অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া ,উপাচার্য, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক চেয়ারম্যান.ট্যুরিজম অ্যান্ড হস্পিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।








