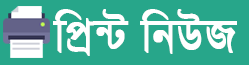জুলাই সনদের আলোকে জাতীয় নির্বাচন সম্ভব?

আমীন আল রশীদ: জুলাই সনদের ভিত্তিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার জামায়াত, এনসিপিসহ আরও কিছু দল। বিএনপিও জুলাই সনদের বিপক্ষে নয়। কিন্তু সনদের কিছু ধারা এবং এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে অন্য দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির পার্থক্য সুস্পষ্ট। জুলাই সনদ কবে স্বাক্ষরিত হবে এবং আদৌ এই সনদের আলোকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে কিনা—তা নিয়ে কিছুটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন হলো, জুলাই সনদের আলোকে জাতীয় নির্বাচন সম্ভব কিনা বা এই সনদের আলোকে নির্বাচন না হলে তার পরিণতি কী হবে?
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গত ৫ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস যে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন—তার ধারাবাহিকতায় এসেছে জুলাই সনদ। যে সনদের চূড়ান্ত খসড়া করতে ৩৫টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন—যে কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা নিজেই।
ধারাবাহিক সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে এবং কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে, মোটা দাগে এরকম বিষয়ের সংখ্যা ৮৪ এবং এখানে অঙ্গীকার আছে ৮টি। কিন্তু এর কিছু সুপারিশ ও অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে যে, এগুলো বাস্তবসম্মত কিনা এবং এগুলোর আলোকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্ভব কিনা?
জুলাই সনদে যেসব বিষয় এসেছে, যেসব সুপারিশ ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ সুপারিশই ভালো এবং এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা দেশের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হবে বা সমাধানের সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ আইনসভা বা সংসদ ও সংবিধান-সম্পর্কিত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন।
সনদের ২১ নম্বরে বলা হয়েছে: ‘সংবিধানে যুক্ত করা হবে যে, (ক) বাংলাদেশে একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকিবে, যাহার নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) ১০০ (একশত) সদস্য নিয়ে নিয়ে গঠিত হইবে।’ (খ) নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation-PR) পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষের ১০০ (একশত) জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। (গ) উচ্চকক্ষের মেয়াদ হইবে শপথ গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বছর। তবে কোনো কারণে নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া গেলে উচ্চকক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে। (ঘ) রাজনৈতিক দলগুলো নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০% নারী প্রার্থী থাকিতে হইবে।’
প্রশ্ন হলো, সনদের এই ধারা বাস্তবায়ন করে জাতীয় নির্বাচন কি সম্ভব? কারণ বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনসভা এককক্ষবিশিষ্ট। এটিকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করতে হলে সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। এটি রাষ্ট্রের একটি মৌলিক পরিবর্তন। শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির একটি অধ্যাদেশ দিয়ে এত বড় একটি পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা—সেই প্রশ্নটি এরইমধ্যে উঠেছে। সুতরাং, জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচন হতে হবে—এই দাবিতে যারা অবিচল, তারা এই সমস্যার কী সমাধান দিচ্ছেন? সংবিধানের এত বড় একটি পরির্ব্তন এবং সংসদের কাঠামোতে পরিবর্তন হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে?
ঐকমত্য হওয়া বিষয়ের ৫২ নম্বরে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে বলা হয়েছে: আইনের দ্বারা নিম্নরূপে গঠিত একটি বাছাই কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা হবে: (১) জাতীয় সংসদের স্পিকার (যিনি এই বাছাই/selection কমিটির প্রধান হবেন), (২) ডেপুটি স্পিকার (যিনি বিরোধী দল হতে নির্বাচিত হবেন), (৩) প্রধানমন্ত্রী, (৪) বিরোধী দলের নেতা, এবং (৫) প্রধান বিচারপতির প্রতিনিধি হিসাবে আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি।
বর্তমানে যে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করছে, অর্থাৎ অভ্যুত্থানের পরে এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করা হয়েছে, সেটি জুলাই সনদে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গঠন করা হয়নি। প্রশ্ন হলো, জুলাই সনদের আলোকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে গেলে কি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে? কিন্তু বর্তমানে যেহেতু সংসদ নেই, স্পিকারও নেই—তাহলে কার নেতৃত্বে বাছাই কমিটি হবে? এই বিধান কি আগামী নির্বাচনের পরে গঠিত সংসদের মেয়াদকালে কার্যকর হবে?
জুলাই সনদে সংসদীয় গণতন্ত্র শক্তিশালী করা এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় বেশ কিছু সুপারিশ রয়েছে। যেমন বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন; সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পদে সংসদে আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে নির্বাচন করা ইত্যাদি। এগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলেও নির্বাচনের আগেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও বিষয় নেই। কেননা স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রশ্নটি আসবে নির্বাচনের পরে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন এবং দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের মতো বিষয়ে নির্বাচনের আগে কী করে সম্ভব—আলোচনাটা সেখানেই।
সংবিধান-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো আগামী জাতীয় সংসদ গঠনের দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের পক্ষে বিএনপি। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী আগামী নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশের মাধ্যমে বা গণভোটের মাধ্যমে এবং এনসিপি গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন চায়। জামায়াত মনে করে, সংস্কার আগামী সংসদের হাতে ছেড়ে দিলে গণঅভ্যুত্থানের প্রতি অবিচার করা হবে। নামমাত্র সংস্কার হলে হবে না। এর আইনি ভিত্তি লাগবে। তার ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। এনসিপি মনে করে, সংস্কার প্রস্তাবগুলোর টেকসই বাস্তবায়নের একমাত্র পথ নতুন সংবিধান। যদি পুরনো সংবিধানই ঘষামাজা করা হয় এবং এটা বাস্তবায়নে পরবর্তী সরকারের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।
বিএনপির প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত। কেননা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে যারা সংসদ ও সরকার গঠন করবে, তারাই সিদ্ধান্ত নেবে সনদ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে। বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার কী হবে। এই মুহূর্তে অধিকাংশ দল সনদ বাস্তবায়নের ব্যাপারে একমত হলেও জনগণ কী চায়, সেটি জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন।
প্রতিটি দলই দাবি করে জনগণ তাদের সঙ্গে আছে। কিন্তু কত শতাংশ জনগণ তাদের সঙ্গে আছে, সেটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ছাড়া জানার কোনও উপায় নেই। অতএব, জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া কোনও আইনি ও সাংবিধানিক পরিবর্তনের সুযোগ নেই। গায়ের জোরে বা জনগণের অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়ে কেউ যদি এটা করতে চায়, তাহলে ভবিষ্যতে প্রতিটি কাজই প্রশ্নের মুখে পড়বে।
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায় কেউ কেউ এ বিষয়ে গণভোট নেওয়ার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে মতামত গ্রহণের পদ্ধতিই হলো গণভোট। এর মাধ্যমে জনগণের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের জন্য উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে গণভোটের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। বরং বাংলাদেশের বাস্তবতায় গণভোটকে ‘একটা বিচিত্র ধরনের নির্বাচন’ হিসেবে আখ্যায়িত করে খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন: এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দুটি কালো বাক্সের মধ্যে। একটি কালো বাক্সে ‘হ্যাঁ’ লেখা। আরেকটিতে ‘না’। অর্থাৎ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় দুই বাক্সের মধ্যে। এই ‘হ্যাঁ’-‘না’ ভোটের নির্বাচনের গোড়াপত্তনকারী পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইউব খান। সরকারি কর্মচারীরাই এই ভোট গ্রহণের দায়িত্বে থাকেন। তাই ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে ‘না’ ভোট পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। (মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাজনীতির তিন কাল, অনন্যা/২০০৩, পৃ. ১৮২)।
বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে তিনটি (১৯৭৭, ১৯৮৫ এবং ১৯৯১) গণভোট হয়েছে, তার প্রত্যেকটি বিতর্কিত হয়েছে। প্রতিটি গণভোটের ফলাফল নিরঙ্কুশভাবে সরকারের পক্ষে গেছে। সরকার যে ফলাফল চেয়েছে, গণভোটের ফলাফলে তার কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি। ভোটের ফলাফলের চিত্রই বলে দেয় এই গণভোটগুলো আসলে কেমন হয়েছে এবং এসব ভোটে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কতটা ছিল।
সুতরাং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন বা সংবিধান সংশোধন এবং সংসদের কাঠামো পরিবর্তনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করা হলে তার ফলাফল কী হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ ওই ভোটে জনগণের মতামতের কতটুকু প্রতিফলন ঘটবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, গণভোটে জনগণের অংশগ্রহণ থাকে অতি সামান্য এবং যে পরিমাণ ভোট পড়ে বলে দাবি করা হয়, সেগুলো আসলে ভোটের দায়িত্বে থাকা সরকারি লোকজনের সৃষ্ট।
কিন্তু এর কোনও কিছুতেই সমাধান না মিললে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, বিশেষ করে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংসদ গঠনের আগেই সাংবিধানিক ও সংসদীয় কাঠামোর সংস্কারের জন্য সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে মতামত চাওয়া যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এর সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।
তাহলে সমাধান কী? সমাধান হলো, জুলাই সনদে সেইসব সুপারিশ ও অঙ্গীকারই যুক্ত করতে হবে যা নিয়ে সব রাজনৈতিক দল একমত হবে এবং একমত না হলে তারা নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে রাখবে। দলগুলো তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে বিষয়গুলো উল্লেখ করবে। যারা সংসদে যাবে, তারা এটার বাস্তবায়ন করবে। তবে যেসব বিষয় সংবিধান সংশোধন বা রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যেমন কিছু আইনি সংস্কার এমনকি পুলিশ কমিশন গঠনের মতো বিষয়গুলো অধ্যাদেশ জারি করেই হতে পারে। কিন্তু জুলাই সনদের আলোকেই আগামী জাতীয় নির্বাচন হতে হবে; সংবিধান ও রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ, গণভোট বা গণপরিষদের মাধ্যমে হতে হবে—এইসব দাবিতে অবিচল থাকলে নির্বাচনটিই দীর্ঘ সময়ের জন্য ঝুলে যেতে পারে, যা দেশকে আরও বড় সংকটের দিতে নিয়ে যাবে।
লেখক: সাংবাদিক
ইত্তেহাদ নিউজ, এয়ার পোর্ট রোড, আবুধাবী ,সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইমেইল: [email protected], web:www.etihad.news
এম এম রহমান, প্রধান সম্পাদক, ইত্তেহাদ নিউজ, এয়ার পোর্ট রোড, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত