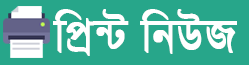সাংবাদিকতায় এআই প্রযুক্তি

২০২০ সালের পর থেকে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের বার্তাকক্ষে এক নতুন পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেছে। সেটি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এর ব্যবহার। প্রযুক্তির এই বিপ্লব সাংবাদিকতাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। আজ আর এআই শুধু প্রযুক্তি খাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ওয়াশিংটন পোস্ট, রয়টার্স, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো বিশ্বখ্যাত মিডিয়া সংস্থাগুলো তাদের দৈনন্দিন কাজে এআইকে সঙ্গী করেছে। প্রশ্ন জাগে, সাংবাদিকতায় এআই প্রযুক্তি এড়িয়ে চলা আদৌ সম্ভব কি?
এআই সাংবাদিকতার অপরিহার্য বাস্তবতা
সাংবাদিকতা হলো দ্রুততম সময়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশনের শিল্প। কিন্তু তথ্যের পাহাড়, সামাজিক মাধ্যমের বিপুল স্রোত, এবং পাঠক–দর্শকের পরিবর্তিত চাহিদা সাংবাদিকদের ওপর অসীম চাপ তৈরি করছে। এই চাপে এআই এক প্রকার সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
সংবাদ কিউরেশন, ফ্যাক্ট চেকিং, অনুবাদ, নিউজলেটার তৈরি, প্রুফরিডিং, শিরোনাম প্রস্তাব—এসব ক্ষেত্রে এআই অল্প সময়ে অনেক কাজ সম্পন্ন করছে। রয়টার্সের নিউজ ট্রেসার যেমন সামাজিক মাধ্যমে ব্রেকিং নিউজ শনাক্ত ও যাচাই করতে সক্ষম তেমনি ওয়াশিংটন পোস্টের হেলিওগ্রাফ সুসজ্জিত ডাটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবাদ তৈরি করছে। ফলে বোঝাই যায়, সংবাদ জগতের প্রতিদিনকার চাহিদা পূরণে এআই কার্যত অনিবার্য হয়ে উঠছে।
এআই ব্যবহারের সুবিধা:
এআই ব্যবহারের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো সময় সাশ্রয়। যে কাজ করতে সাংবাদিকের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগত, এআই তা কয়েক মিনিটে করে দিতে সক্ষম। তাছাড়া পাঠকের আচরণ বিশ্লেষণ করে তাদের উপযোগী করে কনটেন্ট সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। যা সংবাদমাধ্যমকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করছে।
সংবাদ কিউরেশন, ফ্যাক্ট চেকিং, অনুবাদ, নিউজলেটার তৈরি, প্রুফরিডিং, শিরোনাম প্রস্তাব—এসব ক্ষেত্রে এআই অল্প সময়ে অনেক কাজ সম্পন্ন করছে। রয়টার্সের নিউজ ট্রেসার যেমন সামাজিক মাধ্যমে ব্রেকিং নিউজ শনাক্ত ও যাচাই করতে সক্ষম তেমনি ওয়াশিংটন পোস্টের হেলিওগ্রাফ সুসজ্জিত ডাটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবাদ তৈরি করছে।
এছাড়া হেইজেন (HeyGen)-এর মতো প্ল্যাটফর্ম এআই-চালিত অবতার জেনারেটর (AI Avatar Generator) দিয়ে বহু ভাষায় সংবাদ ভিডিও তৈরি করছে। অর্থাৎ সাংবাদিকতা এখন শুধু দ্রুত নয়, বরং আরও বেশি আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তিকৃত হয়ে উঠছে।
চ্যালেঞ্জ ও নৈতিকতা:
এআই ব্যবহারের সুবিধার পাশাপাশি এর নৈতিক চ্যালেঞ্জও প্রবল। অ্যালগরিদম যতটুকু ডাটা দিয়ে প্রশিক্ষণ পায়, ততটুকুই প্রতিফলন ঘটায়। যদি ডাটায় পক্ষপাত থাকে, তবে সেই পক্ষপাতই সংবাদে প্রতিফলিত হবে। এতে সাংবাদিকতার নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।
গার্ডিয়ানের এডিটর পল চ্যাডউইক সতর্ক করে বলেছেন, ‘এআই ব্যবহার করলে সাংবাদিকদের সব সময় ভাবতে হবে, এটি কতটা নৈতিকতার মানদণ্ডের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। একইসঙ্গে স্বচ্ছতার অভাবও বড় ঝুঁকি। পাঠক জানতেই পারে না সংবাদটি মানবসৃষ্ট না মেশিনসৃষ্ট। ফলে আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে’।
একই প্রসঙ্গে সচিতা নিশাল, শার্লট লি এবং নিকোলাস ডায়াকোপোলস (২০২৪) [Sachita Nishal, Charlotte Li & Nicholas Diakopoulos (2024)] সালে তাদের গবেষণা Domain-Specific Evaluation Strategies for AI in Journalism (arXiv) নিবন্ধে বলেন, ‘News organizations today rely on AI tools to increase efficiency …However, practitioners also express reservations …due to the technical and ethical challenges involved in evaluating AI technology and its return on investments’.
অর্থাৎ ‘বর্তমানে সংবাদসংস্থাগুলো দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এআই টুলের ওপর নির্ভর করছে… তবে ব্যবহারকারীরা একইসঙ্গে সংশয় প্রকাশ করছেন… কারণ এআই প্রযুক্তি মূল্যায়ন এবং এতে বিনিয়োগের প্রতিফলন যাচাই করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।’
কর্মসংস্থানের সংকট:
এআই ব্যবহারের আরেকটি বড় বিতর্ক হলো চাকরি নিয়ে। ২০২৩ সালে জার্মানির এক্সেল স্প্রিঙ্গার গ্রুপ বিল্ড ও দায়ে ওয়েল্ট পত্রিকায় কর্মী ছাঁটাই করেছে। যুক্তি হলো, সাংবাদিকের অনেক কাজ এখন এআই-ই করতে সক্ষম। খেলার ফলাফল, কর্পোরেট আয়ের রিপোর্ট, এমনকি আবহাওয়ার খবরে মানুষ নয়, মেশিন কাজ করছে। এতে স্পষ্ট, সাংবাদিকতার অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে।
এই প্রসঙ্গে পেনা-ফার্নান্দেজ প্রমুখ (২০২৫) [Peña-Fernández et al. (2025)] সালে তাদের গবেষণা Can artificial intelligence replace journalists? A theoretical approach (Frontiers in Communication) নিবন্ধে বলেন, ‘AI does not replace the essence of the journalist as a narrator, analyst and interpreter. …This synergistic model can redefine journalism as a more efficient and innovative practice, but without compromising its core values.’
অর্থাৎ ‘এআই সাংবাদিকের মূল সত্তাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না, কারণ এটি একজনকে বর্ণনাকারী, বিশ্লেষক এবং ব্যাখ্যাকারী হিসেবে উপস্থাপন করে, ব্যক্তি হিসেবে না। …এই সমন্বিত মডেল সাংবাদিকতাকে আরও দক্ষ ও উদ্ভাবনী চর্চা হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করতে পারে, তবে এর মূল মূল্যবোধের সাথে আপস না করেই।’
ফেক নিউজ ও ডিপফেকের ঝুঁকি:
এআই যুগের আরেকটি বড় আশঙ্কা হলো ফেক নিউজ ও ডিপফেক। এআই মুহূর্তে অসংখ্য ভুয়া ছবি, ভিডিও বা ভয়েস রেকর্ড তৈরি করে ছড়িয়ে দিতে পারে। এতে শুধু ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। যদিও ফ্যাক্ট চেকিং টুল-এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, তবে ভুয়া তথ্যের স্রোত এত বেশি যে তা সামাল দেওয়া কঠিন।
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নতুন দিগন্ত:
ঝুঁকি থাকলেও এআই সাংবাদিকতার জন্য এক বিশাল সুযোগও বটে। বিশাল ডেটাবেস থেকে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা, অজানা যোগসূত্র তৈরি করা। এসব কাজ এআই সাংবাদিকদের হাত শক্ত করছে। সরকারি কেনাকাটায় দুর্নীতি, রাজনৈতিক অনিয়ম কিংবা কর্পোরেট কারচুপির প্রমাণ এআই সহজেই উন্মোচন করতে পারে। ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এটি এক বিপ্লব ডেকে আনতে পারে।
এআই ব্যবহার সাংবাদিকের বিকল্প নয়, বরং সহায়ক হওয়া উচিত। এজন্য সাংবাদিক ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক থাকা দরকার। অপেক্ষাকৃত কম সার্কুলেটেড সংবাদপত্র কিংবা ফ্রিল্যান্সাররা ওপেন সোর্স টুল ব্যবহার করে কাজ সহজ করতে পারে। একইসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।
গুগল ইতিমধ্যেই সাংবাদিকদের জন্য শিরোনাম প্রস্তাব বা রিপোর্ট তৈরির সহায়ক এআই তৈরি করছে। তবে সাংবাদিকদের সুরক্ষা ইউনিয়নগুলো ঢেলে সাজাতে হবে। তাদের জোর দিতে হবে চাকরি রক্ষা ও নৈতিক মানদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখার ওপর।
এআই এড়ানো কি সম্ভব?
এখন প্রশ্নে ফিরে আসি, সাংবাদিকতায় এআই এড়ানো সম্ভব কি? বাস্তবতা হলো, সাংবাদিকতা যেভাবে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠছে, তাতে এআইকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। ইন্টারনেট যেমন একদিন সংবাদমাধ্যমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল, তেমনি এআইও হবে। কিন্তু মূল পার্থক্য হলো, এআই ব্যবহারে নৈতিকতা, স্বচ্ছতা এবং মানবীয় তত্ত্বাবধান অপরিহার্য। সাংবাদিকের আবেগ, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা কোনো যন্ত্রই প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। তাই ভবিষ্যতের সাংবাদিকতা হবে মানব–এআই সহযোগিতার সমন্বিত রূপ।
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে এআই-এর প্রভাব:
বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংবাদমাধ্যমে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সংবাদ সংগ্রহ, লেখা, সম্পাদনা, ভিডিও প্রোডাকশন কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট—সবক্ষেত্রেই এআই-এর প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে।
এআই-কে ভয় না পেয়ে সাংবাদিকদের উচিত এর ব্যবহারকে প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজে লাগানো। সঠিক নীতিমালা, ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থার জোরদার প্রয়োগ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাতে পারলে এআই বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে আরও আধুনিক, গতিশীল ও পাঠককেন্দ্রিক করে তুলবে।
একদিকে এআই সংবাদকর্মীদের কাজ সহজ করছে। তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য বিশ্লেষণ, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, ট্রেন্ড চিহ্নিতকরণ কিংবা স্বল্প সময়ে খসড়া সংবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তি সাংবাদিকদের সময় ও শ্রম বাঁচিয়ে দিচ্ছে। অনলাইন পোর্টালগুলোয় রিয়েল-টাইম আপডেট ও স্বয়ংক্রিয় কনটেন্ট সাজেস্ট করার মাধ্যমে পাঠক টানার কৌশলও এআই-এর অবদান।
অন্যদিকে, চ্যালেঞ্জও কম নয়। ভুয়া সংবাদ বা ডিপফেক কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বেড়েছে। সম্পাদকীয় স্বাধীনতা ও সাংবাদিকতার মৌলিক নীতিগুলো প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে যদি প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। এছাড়া চাকরির বাজারে প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে, কারণ অনেক প্রতিষ্ঠানে স্বয়ংক্রিয়তার ফলে মানবসম্পদ সংকোচনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।
তবে এআই-কে ভয় না পেয়ে সাংবাদিকদের উচিত এর ব্যবহারকে প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজে লাগানো। সঠিক নীতিমালা, ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থার জোরদার প্রয়োগ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটাতে পারলে এআই বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে আরও আধুনিক, গতিশীল ও পাঠককেন্দ্রিক করে তুলবে।
এআই সাংবাদিকতাকে যেমন গতিশীল করছে, তেমনি নতুন ঝুঁকিও তৈরি করছে। এর সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হবে, তবে চোখ বন্ধ করে নয়। প্রতিটি পদক্ষেপে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলতে হবে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। আর পাঠকের আস্থা রক্ষা করতে হবে। সুতরাং, সাংবাদিকতায় এআই প্রযুক্তি এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। বরং এটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাই হবে আগামী দিনের বড় চ্যালেঞ্জ—যেখানে প্রযুক্তি থাকবে সাংবাদিকের সহায়ক, প্রতিস্থাপক।
রেফারেন্স:
১। Brigham, N. G., Lerman, K., & Olteanu, A. (2024). Developing story: Case studies of generative AI's use in journalism. arXiv preprint arXiv:2406.13706. https://arxiv.org/abs/2406.13706
২। Tseng, E., Young, M., Chang, J., Li, L., & Li, J. (2025). Ownership, not just happy talk: Co-designing a participatory large language model for journalism. arXiv preprint arXiv:2501.17299. https://arxiv.org/abs/2501.17299
৩। Nishal, S., Li, C., & Diakopoulos, N. (2024). Domain-specific evaluation strategies for AI in journalism. arXiv preprint arXiv:2403.17911. https://arxiv.org/abs/2403.17911
৪। Anagnostopoulou, A., Gouvea, T., & Sonntag, D. (2024). Enhancing journalism with AI: A study of contextualized image captioning for news articles using LLMs and LMMs. arXiv preprint arXiv:2408.04331. https://arxiv.org/abs/2408.04331
৫। Peña-Fernández, S., Rodríguez-Castro, M., & López-García, X. (2025). Can artificial intelligence replace journalists? A theoretical approach. Frontiers in Communication, 10, 1537146. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1537146
প্রশান্ত কুমার শীল : শিক্ষক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক
ইত্তেহাদ নিউজ, এয়ার পোর্ট রোড, আবুধাবী ,সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইমেইল: [email protected], web:www.etihad.news
এম এম রহমান, প্রধান সম্পাদক, ইত্তেহাদ নিউজ, এয়ার পোর্ট রোড, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত