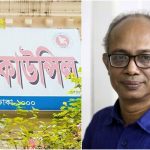গণ-সর্বনাশে মচ্ছব চলছে!
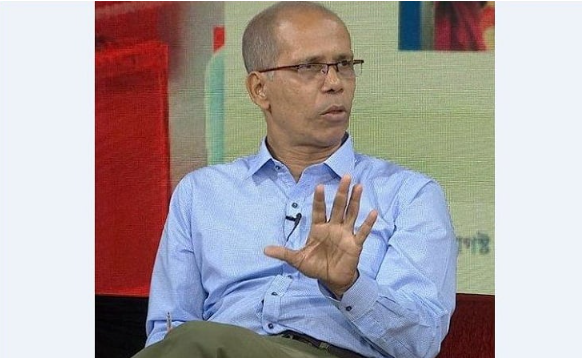
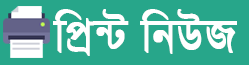
আলম রায়হান: বছর দুই আগে কৃষির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পৃক্ত হয়েছি। কারণ হতে পারে দুটি। এক. পেশায় অধিকতর বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া; দুই. জীবনের গোধূলি বেলায় ভিন্ন কিছু করার মানবকুলের ইনবিল্ড প্রবণতা। পড়ন্ত বেলায় ‘কাজ নেই তো খৈ ভাজ’ ধারায় কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দেখলাম, সবার চোখের সামনে গণ-সর্বনাশে মচ্ছব চলছে! কচ্ছপগতিতে কৃষিতে নানান ধরনের অনাচার প্রবেশ করানোর কৌশলী ধারায় সব ধরনের ফসলে বিষ প্রয়োগের তাণ্ডব এখন তুঙ্গে। আগাছা দমনেও ব্যবহার করা হয় বিষ। যার বাহারি নাম, বালাইনাশক। এর প্রভাবে বহু আগেই প্রকৃতির লাঙলখ্যাত কেঁচো নিঃশেষ। বহুল প্রচলিত ডায়ালগ, ‘মায়ের ভোগে গেছে!’ আগে যেখানে জুতসই স্থানে এক কোপ দিলে দশটা কেঁচো পাওয়া যেত, সেখানে এখন দশ কোপ দিলেও একটা কেঁচো মেলে না। বিষয়টি কয়েক দিন আগে হাতে-কলমে টের পেয়েছি। শখের মৎস্যশিকারি সাংবাদিক নোমানী আমাকে কয়েকটা কেঁচো নিয়ে আসতে বলেছিল। পুকুর আমার, কেঁচোও আমাকে দিতে হবে। আহ্লাদ! কিন্তু কয়েকটা কোপ দিয়েও একটি কেঁচোও পাওয়া যায়নি। এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে! অথচ বৈজ্ঞানিকভাবেই বলা আছে, প্রাকৃতিক লাঙল মাটিতে কেঁচো ক্ষুদ্রাকৃতির টানেল তৈরি করে। যাতে মাটির ভেতরে বাতাস ও পানির প্রবাহ থাকে। মাটির ওপরের অংশেও কেঁচোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ফসল চাষ, মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিসহ ছোটখাটো অনেক পাখি ও প্রাণীর আহার হিসেবে কেঁচোর গুরুত্ব অপরিসীম। কেঁচোর সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টি জীববৈচিত্র্যের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
কেঁচো নিয়ে নিজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কয়েক দিন পর কুমিল্লার মডেলে ‘বর্ষার জলে মৎস্য চাষ’ প্রচেষ্টার আলে গিয়ে অনেক শামুকের খোসা দেখলাম। আনন্দের অনুভূতি হলো, কেঁচো না থাকলেও শামুক এখনো আছে! না হলে খোসা এলো কোথা থেকে? কিন্তু কিছু পরেই আতঙ্কিত হয়েছি। কারণ ভরাবর্ষায় শামুক মরার তো কথা নয়। আর মৃত শামুকের খোসাগুলো ছিল ছোট শামুকের। খবর নিয়ে জানা গেল, কাছাকাছি জমিতে আগাছা দমনের জন্য বালাইনাশক নামের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। হয়তো এতে আক্রান্ত হয়ে শামুকগুলো পানি ছেড়ে কোনোরকম আলে উঠেছে। কিন্তু বাঁচেনি। ভাবলাম, কী সর্বনাশ! এ ভাবনায় তাড়িত থাকা অবস্থায় বরিশাল সদর উপজেলার কৃষকদের এক কর্মশালায় যোগ দিয়েছিলাম কৃষক হিসেবে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বরিশাল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন নানান প্রসঙ্গ টেনে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা পুলিশ সুপার মো. শরিফ উদ্দীন কৃষির ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ‘আমরা আমাদের পরিবেশ নষ্ট করছি।’ উল্লেখ্য, মো. শরিফ উদ্দীন কৃষিবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র।
হালের কৃষক হিসেবে আমার স্বল্প সময়ের অভিজ্ঞতা এবং বরিশাল জেলার প্রধান দুই কোতোয়ালের বক্তব্য এক সরল রেখায় দাঁড় করালে উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে উঠবে। কারণ, আমরা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করছি না এবং কৃষির ক্ষেত্রে ভয়াবহ মাত্রায় পরিবেশ নষ্ট করেই চলেছি। আর এর মূলে রয়েছে কথিত ‘বালাইনাশক’, যা আসলে ভয়ানক বিষ।
প্রসঙ্গত, বালাইনাশকের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার পদ্ধতির তালিকা বেশ দীর্ঘ, যা অনুসরণ করা আমাদের দেশের কৃষকদের পক্ষে তো দূরের কথা, বিসিএস কর্মকর্তারাও পারবেন কি না; সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই কৃষকদের দোষারোপ করে লাভ কী? বলা হয়, ক্ষতির মাত্রা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে বালাইনাশকের প্রকৃতি, মাত্রা, ব্যবহার পদ্ধতি, পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, সূর্যালোকসহ নানান বিষয়ের ওপর। বিতরণ করা জ্ঞান অনুসারে, সুফল পেতে হলে যে কোনো বালাইনাশক স্প্রে করতে চারটি মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলা উচিত। এগুলো হলো, সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন, সঠিক ডোজ বা মাত্রা নির্ধারণ, সঠিক সময় নির্বাচন এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ। কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটিই করা হয় না। বরং ‘যত গুড় তত মিঠা’ প্রবচন বিবেচনায় রেখেই অতিরিক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যয়বহুল হওয়ার পাশাপাশি সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটেই চলেছে। সঙ্গে সামগ্রিক পরিবেশের সর্বনাশ তো আছেই। আর প্রকৃতিতে বিদ্যমান উপকারী ও বন্ধু পোকা ধ্বংস করার ফলে শত্রু পোকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ফলে পরাগায়নের সহায়কের অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে।
অবশ্য কথিত ‘সঠিক মাত্রায়’ প্রয়োগ করা হলেও সর্বনাশ হবেই। যা খাদ্য, মাটি, পানির ওপর ভয়ংকর প্রভাব ফেলার পাশাপাশি প্রয়োগকারীর ওপরও গুরুতর প্রভাব ফেলে। তাৎক্ষণিক প্রভাবের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে ক্যান্সার, টিউমার, ত্রুটিপূর্ণ সন্তান জন্ম দেওয়া, বন্ধ্যত্ব, অন্যান্য প্রজননগত সমস্যা, প্রস্টেটের সমস্যা, লিভার, কিডনি, ফুসফুস এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিগুলো বালাইনাশক ব্যবহারের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর পরও দেখা দিতে পারে। তখন এগুলো যে বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে হয়েছে, তা আর বিবেচনায় আসে না। তখন হয়তো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায় কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতার পঙক্তি, ‘কী বিষে দংশিল লখাইরে…।’
প্রসঙ্গত, প্রয়োগকৃত বালাইনাশকের শতকরা ৯৮ ভাগ এবং আগাছানাশকের ৯৫ ভাগই বাতাস, পানি ও মাটিতে মিশে যায়। বালাইনাশকের অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে মাটি, বায়ু, পানি প্রভৃতি দূষণ হয়। বিশেষ করে পুকুর, জলাধার, খাল-বিল, নদী-নালা এবং এতে থাকা মাছ ও জলজ প্রাণী, ফাইটোপ্লাংটন, জুপ্লাংটন, জলজ উদ্ভিদ, ব্যাঙ ইত্যাদি আক্রান্ত হচ্ছে। এ পানি ব্যবহারকারী লোকজন ও গবাদি পশুও বালাইনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। ভূপরিস্থ পানির সঙ্গে সঙ্গে মাটির নিচে আর্সেনিক দূষিত পানিতে এরই মধ্যে বালাইনাশকের বালা বাসা বেঁধেছে কি না, কে জানে! পানীয় জল বিষাক্ত হয়ে ভয়ানক মাত্রায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। পরাগায়নকারী প্রাণী যেমন—মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গদের ওপরও বিষাক্ত প্রভাব ফেলেছে বালাইনাশক। পাখি ও পাখিজাতীয় প্রাণীও বালাইনাশকের কারণে বিপদে আছে। শকুনের সংখ্যা হ্রাসের জন্য গবাদি পশুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাইক্লোফেনাক নামক ওষুধের ব্যবহারকে দায়ী করা হয়। কিন্তু এখনো তো আর মরা গরু মাঠে ফেলে দেওয়া হয় না। মরার আলামত হলেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মরার পরও ‘হালাল’ শ্রেণিভুক্ত হয়ে যায়। জবাই করা গরু মানুষ খায়, উচ্ছিষ্ট খেত কাক। ধারণা করা হয়, এই উচ্ছিষ্ট খেয়েই কাক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাক গেল কোথায়? নাসিরউদ্দিন হোজ্জার গল্প অনুসারে কাক কি অন্য শহরে গেছে! তা তো নয়। এই কাক নিয়ে এখনো কেউ কা-কা করছেন না! দীর্ঘ ব্যবহারে পোকামাকড় বালাইনাশকের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। ফলে আরও শক্তিশালী বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে, যা পরিবেশের জন্য আরও ক্ষতি ডেকে আনছে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত অনুমোদিত বালাইনাশকের ‘নিরাপদ কাল’ অর্থাৎ ফসলে বালাইনাশক প্রয়োগের পর নিরাপদকাল সাধারণত এক থেকে পঁচিশ-ত্রিশ দিন পর্যন্ত হতে পারে। তবে কোনো কোনো বিষের ক্ষেত্রে এমন কোনো নিরাপদ কাল নাও থাকতে পারে বলে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এরপরও প্রায় সব ফল-ফসলে বালাইনাশক নামের বিষ প্রয়োগ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু কিছু সবজি উৎপাদনে প্রায় প্রতিদিনই কীটনাশক স্প্রে করা হয়। মানুষ তা প্রতিনিয়ত খাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ফলের রাজা আম। চার-পাঁচবার হাতবদল হওয়া আমবাগানে অন্তত ১৫ থেকে ১৬ বার কথিত বালাইনাশক স্প্রে করা হয়। এক দশক আগেও দুই-তিনবার বালাইনাশক ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া গেছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাবে মাটিতে থাকা কেঁচো, শতধরনের অন্যান্য পোকামাকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে মাটির ভৌতিক ও রাসায়নিক গুণাবলি নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হয়েছে ভূমির উর্বরতার। অতি প্রয়োগকৃত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত খাদ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষ। আক্রান্ত হচ্ছে নানান জটিল রোগে। এদিকে দায়সারা গোছের নানান সাবধানতা অবলম্বনের জন্য প্রয়োগকারীকে মাস্ক ও অ্যাপ্রন পরার নসিয়ত করা হয়। কিন্তু কজন মাস্ক পরেন? অ্যাপ্রন তো অনেক দূরের কথা। সবচেয়ে বড় কথা, বালাইনাশকের নামে ফসলে মাত্রাতিরিক্ত বিষ প্রয়োগ নিয়ে কার্যকরভাবে ভাবছে কে? ঠেকানো অনেক দূরের বিষয়! আর চাইলেই কি ঠেকানো সহজ! ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টায়ই তো সরকার নাকাল হয়েছে। এরপরও পূর্ণ সাফল্য আসেনি।
কারও কারও মতে, কথিত বালাইনাশকের প্রভাব হতে পারে রেডিয়ামের কাছাকাছি। উল্লেখ্য, এখন যেমন আমাদের কৃষি উৎপাদনে বালাইনাশক নামের বিষ ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রায় সেরকমই সবকিছুতে রেডিয়াম ব্যবহারের হুজুগ শুরু তুঙ্গে উঠেছিল এবং রেডিয়ামের অপরীক্ষিত ব্যবহার কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় খোদ আমেরিকাতেই। ১৮৯৮ সালের ২১ ডিসেম্বর মেরি কুরি ও তার স্বামী পিয়েরে কুরি আবিষ্কৃত রেডিয়াম ব্যবহার শুরু হয় ১৯১৭ সালে। ঘড়ি দিয়ে শুরু। অন্ধকারে ঘড়ি দেখার সুবিধার জন্য ঘড়ির ডায়াল ও কাঁটায় রেডিয়াম জনব্যবহৃত শুরু হয়। এসব ঘড়ি আভিজাত্য ও শৌখিনতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এমনকি বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে রেডিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করার জন্য রেডিয়াম মিশ্রিত পানি পান করানো হতো। এ ছাড়া নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী যেমন টুথপেস্ট, প্রসাধনী প্রভৃতিতে রেডিয়ামের ব্যবহার শুরু হয়। নারীরা ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসেবেও রেডিয়াম ব্যবহার করতে শুরু করেন। অনেকে চুল, চোখের পাতা, দাঁত, নখ ও ঠোঁটে রেডিয়ামের প্রলেপ লাগাতেন। যৌনকর্মীরা ব্যবহার করতেন খদ্দেরের মূল আকর্ষণ কেন্দ্রে। কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই দানবীয় সর্বনাশ সামনে চলে আসে। ১৯২৭ সালে গ্রেস ফ্রেইয়ার নামের ক্ষতিগ্রস্ত এক নারী শ্রমিক আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত ঘড়ি তৈরির কারখানায় অরক্ষিত অবস্থায় রেডিয়ামের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই সময় সারা বিশ্বের মানুষ রেডিয়ামের ভয়াবহতার কথা জানতে পারে। কিন্তু ততদিনের অনেক দেরি হয়ে গেছে। মিথ আছে, রেডিয়ামের প্রভাবে মৃতদের কবরে এখনো রেডিয়াম আলো ছড়ায়!
বাস্তবতা হচ্ছে, রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহারে ক্ষতি থেকে কোনো কিছুই রেহাই পাচ্ছে না। ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাটি, পানি, বায়ু ও উপকারী কীটপতঙ্গ। কৃষিজমি বিশেষ করে ধানের জমিতে একসময় শামুক-ঝিনুক ও ছোট মাছ দেখা যেত। এখন এগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। ফসলের জমিতে পোকামাকড় খাওয়ার জন্য পাখপাখালির বিচরণ এখন অনেকটাই অতীতের গালগপ্পের মতো শোনায়। ফল-ফসলের মাঠে ব্যস্ত ভ্রমরের ভন ভন অথবা মৌমাছির গুঞ্জন নেই। এ ছাড়া বিলুপ্তপ্রায় কৃষি পরিবেশে নানারকম সরীসৃপ। প্রসঙ্গত, রাসায়নিক সার উৎপাদন ও আমদানি ধারায় আছে। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রপ প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে, দেশে পেস্টিসাইডের বাজার ৫ হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে দানাদার বাদে তরল ও পাউডার পেস্টিসাইডের প্রায় পুরোটাই আমদানি করা হয়। আর এই ব্যবসার ৫৫ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি। আর কোণঠাসা হয়ে পড়ছে দেশীয় প্রায় সাড়ে ছয়শ প্রতিষ্ঠান। প্রশ্ন হচ্ছে, রাসায়নিক সার ও কথিত বালাইনাশকের বালা-মসিবত থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব কবে? আমরা কি শকুনের পথে হাঁটছি! আবিষ্কারক কুরি দম্পতি রেডিয়ামের ক্ষতিকর বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু সর্বনাশ হওয়ার আগে তার সাবধানবাণীতে কান দেওয়া হয়নি। আমাদের দেশে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের বিষয়ে ‘মিউ মিউ’ সাবধানবাণীতে কে কান দিচ্ছে? অবশ্য, রাজনীতির ঢোলের শব্দ দূষণ অতিক্রম করে বালাইনাশকের পরিবেশ দূষণের সাবধানবাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করার কথাও না!
লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক
সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সব সংবাদ, ছবি ,অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও লেখা পেতে আমাদের ফেসবুক পেইজে লাইক দিয়ে অ্যাকটিভ থাকুন। ভিজিট করুন : http://www.etihad.news
* অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইত্তেহাদ নিউজে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায় ।